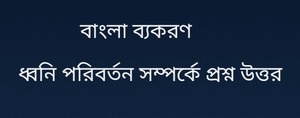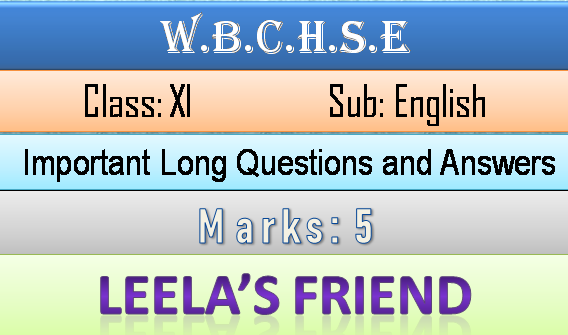এখানে ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর শেয়ার করা হলো।
ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর
প্রশ্ন ১ ধ্বনি পরিবর্তনের দুটি কারণ লেখো।
উত্তর: ধ্বনি পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান দুটি কারণ হল, বাগ্যন্ত্রের ত্রুটি এবং জিভের শিথিলতা বা দুর্বলতা, আর অপেক্ষাকৃত কঠিন কিংবা জটিল শব্দকে সহজ করার প্রবণতা।
প্রশ্ন ২ ধ্বনি পরিবর্তন কতপ্রকার ও কী কী?
উত্তর: ধ্বনি পরিবর্তন সাধারণত চারপ্রকার- (১) ধ্বনির আগমন, (২) ধ্বনির লোপ, (৩) ধ্বনির রূপান্তর, এবং (৪) ধ্বনির স্থানবদল বা স্থানান্তর।
প্রশ্ন ৩ ধ্বন্যাগম কাকে বলে?
উত্তর: উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের প্রথমে, মধ্যে কিংবা অন্ত্যে নতুন একটি স্বরধ্বনির বা ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে ধ্বন্যাগম বলে। যেমন- স্কুল > ইস্কুল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা প্রভৃতি।
প্রশ্ন ৪ স্বরাগম কতপ্রকার ও কী কী?
উত্তর: স্বরাগম তিনপ্রকার- (১) আদিস্বরাগম, (২) মধ্যস্বরাগম, এবং (৩) অন্ত্যস্বরাগম।
প্রশ্ন ৫ আদিস্বরাগম, মধ্যস্বরাগম, অন্ত্যস্বরাগম-এর একটি করে উদাহরণ দাও।
উত্তর:
আদিস্বরাগম: স্কুল > ইস্কুল,
মধ্যস্বরাগম: রত্ন > রতন,
অন্ত্যস্বরাগম: বেঞ্চ > বেঙ্কি।
প্রশ্ন ৬ আদিস্বরাগম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: শব্দের প্রথমে বা আদিতে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে আদি-স্বরাগম বলে।
উদাহরণ: স্কুল > ইস্কুল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা প্রভৃতি।
প্রশ্ন ৭ মধ্যস্বরাগম বা স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ শব্দটির অর্থ হল স্বরের সহযোগে বিভাগ। এ ছাড়াও কবিতায় ছন্দ রক্ষা কিংবা সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য স্বরধ্বনির আগমন ঘটে, বলে এর আরেক নাম বিপ্রকর্ষ।
উদাহরণ: রত্ন (র্ + অত্ + ন্ + ও) > রতন (র্ + অ + ত্ + অ-ন)। এভাবেই ধর্ম > ধরম, কর্ম > করম, গ্রাম > গেরাম প্রভৃতি।
প্রশ্ন ৮ অন্ত্যস্বরাগম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: শব্দের শেষে বা অন্ত্যে অতিরিক্ত স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে অন্ত্যস্বরাগম বলে।
উদাহরণ: ইঞ্চ > ইঞ্চি, বেঞ্চ > বেঞ্চি ইত্যাদি।
প্রশ্ন ৯ ব্যঞ্জনাগম বলতে কী বোঝ?
উত্তর: উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের মধ্যে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগমনকে ব্যঞ্জনাগম বলে। যেমন- উপকথা > রূপকথা, নানা > নানান ইত্যাদি।
প্রশ্ন ১০ ব্যঞ্জনাগম কতপ্রকার ও কী কী?
উত্তর: ব্যঞ্জনাগম তিনপ্রকার- (১) আদিব্যঞ্জনাগম, (২) মধ্যব্যঞ্জনাগম, এবং (৩) অন্ত্যব্যঞ্জনাগম।
প্রশ্ন ১১ মধ্যব্যঞ্জনাগম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: জিভের অসতর্কতাবশত অথবা শ্রুতিমাধুর্যের জন্য শব্দের দুটি ধ্বনির মাঝে একটি অতিরিক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে মধ্যব্যঞ্জনাগম বলে।
উদাহরণ: অম্ল > অম্বল, বানর > বান্দর ইত্যাদি।
প্রশ্ন ১২ অন্ত্যব্যঞ্জনাগম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: শব্দের অন্ত্যে বা শেষে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে অন্ত্যব্যঞ্জনাগম বলে।
উদাহরণ: নানা > নানান, বহু > বহুল ইত্যাদি।
প্রশ্ন ১৩ ধ্বনিলোপ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: শব্দের মধ্যে থাকা যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে তার মধ্যে একটি স্বরধ্বনি এনে যোগ করে উচ্চারণ করার প্রবণতাকে ধ্বনিলোপ বলে।
উদাহরণ: অলাবু > লাউ, জানালা > জানলা।
প্রশ্ন ১৪ ধ্বনিলোপের কারণ কী?
উত্তর: ধ্বনিলোপ একাধিক কারণে ঘটে থাকে। উচ্চারণের ত্রুটি, শ্বাসাঘাতের অস্বাভাবিকতা, অসাবধানতা, অনুকরণ, বাগ্যন্ত্রের ত্রুটি প্রভৃতি।
প্রশ্ন ১৫ ধ্বনিলোপ কতপ্রকার ও কী কী?
উত্তর: ধ্বনিলোপ দু-প্রকার- (১) স্বরধ্বনিলোপ এবং (২) ব্যঞ্জনধ্বনিলোপ।
প্রশ্ন ১৬ স্বরধ্বনিলোপ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: কোনো শব্দ থেকে স্বরধ্বনি লুপ্ত হলে তাকে স্বরধ্বনিলোপ বলে।
প্রশ্ন ১৭ স্বরধ্বনিলোপ কতপ্রকার ও কী কী?
উত্তর: শব্দের মধ্যে অবস্থানভেদে স্বরধ্বনিলোপ তিনপ্রকার- (১) আদিস্বরলোপ, (২) মধ্যস্বরলোপ, এবং (৩) অন্ত্যস্বরলোপ।
প্রশ্ন ১৮ আদিস্বরলোপ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: সচরাচর শব্দের প্রথমে বা আদিতে শ্বাসাঘাত না থেকে যখন মাঝের কোনো ধ্বনিতে শ্বাসঘাত পড়ে, তখন শব্দের গোড়ার স্বরধ্বনিটি দুর্বল হতে হতে একসময় লোপ পায়, তাকেই আদিস্বরলোপ বলে। যেমন- অছিল > ছিল, অলাবু > লাউ, অতসী > তিসি, উডুম্বর > ডুমুর প্রভৃতি।
প্রশ্ন ১৯ মধ্যস্বরলোপ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়লে শব্দের মাঝখানে থাকা স্বরধ্বনিটি ক্রমশ দুর্বল হয়ে একসময় লোপ পায়, তাকেই মধ্যস্বরলোপ বা সম্প্রকর্ষ বলে। যেমন- কলিকাতা > কলকাতা, নাতিজামাই > নাজ্জামাই, গামোছা > গামছা, বসতি > বস্তি প্রভৃতি।
প্রশ্ন ২০ অন্ত্যস্বরলোপ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: উচ্চারণের সময় অনেক ক্ষেত্রে শব্দের প্রথমে যে শ্বাসের জোর থাকে সেটি ক্রমশ কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে না, ফলে একদম শেষের স্বরধ্ব্বনিটি উচ্চারিত না-হওয়ায় লোপ পায়। একেই অন্ত্যস্বরলোপ বলে। যেমন- রাশি > রাশ, অগ্র > আগ, নরঃ > নর, মনুষ্য > মানুষ প্রভৃতি।
ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর
প্রশ্ন ২১ ব্যঞ্জনধ্বনিলোপ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: কোনো শব্দ থেকে ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হলে তাকে ব্যঞ্জনধ্বনিলোপ বলে। যেমন- পাটকাঠি > পাকাঠি, গ্রাম > গাঁ ইত্যাদি।
প্রশ্ন ২২ ব্যঞ্জনধ্বনিলোপ কতপ্রকার ও কী কী?
উত্তর: অবস্থানভেদে ব্যঞ্জনধ্বনিলোপ তিনপ্রকার- (১) আদিব্যঞ্জনলোপ, (২) মধ্যব্যঞ্জনলোপ, এবং (৩) অন্ত্যব্যঞ্জনলোপ। আর সমাক্ষরলোপও ব্যঞ্জনলোপেরই পর্যায়ভুক্ত।
প্রশ্ন ২৩ আদিব্যঞ্জনলোপ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: শব্দের প্রথমে বা আদিতে থাকা ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হলে তাকে আদিব্যঞ্জনলোপ বলে। যেমন- স্থান > থান, স্থিতু > থিতু ইত্যাদি।
প্রশ্ন ২৪ মধ্যব্যঞ্জনলোপ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: শব্দের মধ্যস্থানে থাকা কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হলে তাকে মধ্যব্যঞ্জনলোপ বলে। যেমন- পাটকাঠি > পাকাঠি, ফলাহার > ফলার ইত্যাদি।
প্রশ্ন ২৫ অন্ত্যব্যঞ্জনলোপ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: কোনো শব্দের অন্ত্য বা শেষ থেকে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হলে তাকে অন্ত্যব্যঞ্জনলোপ বলে। যেমন- সখী > সই, নাহি > নাই, গাত্র > গা।
প্রশ্ন ২৬ সমাক্ষরলোপ বলতে কী বোঝ?
উত্তর: কোনো শব্দের মধ্য থেকে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমধ্বনির একটি লুপ্ত হলে তাকে সমাক্ষরলোপ বলে। যেমন- বড়োদাদা > বড়দা, ছোটোদিদি > ছোটদি, পটললতা > পলতা ইত্যাদি।
প্রশ্ন ২৭ ধ্বনির রূপান্তর কতপ্রকার ও কী কী?
উত্তর: ধ্বনির রূপান্তর দু-প্রকার- (১) স্বরধ্বনির রূপান্তর এবং (২) ব্যঞ্জনধ্বনির রূপান্তর।
প্রশ্ন ২৮ স্বরসংগতি বলতে কী বোঝ?
উত্তর: ‘স্বরসংগতি’ শব্দের অর্থ বিভিন্ন ধরনের স্বরের মধ্যে সমতাবিধান। শব্দের মধ্যে একাধিক স্বরধ্বনি থাকলে একটির প্রভাবে অন্যটি বদলে যায়, আবার কখনও পরস্পরের প্রভাবে উভয়েই পরিবর্তিত হয়ে ধ্বনিসাম্য লাভ করে। ধ্বনি পরিবর্তনের ভাষায় একেই স্বরসংগতি বলে। যেমন- দেশি > দিশি, ফিতা > ফিতে প্রভৃতি।
প্রশ্ন ২৯ স্বরসংগতি কতপ্রকার ও কী কী?
উত্তর: স্বরধ্বনি পরিবর্তনের অভিমুখ অনুসারে স্বরসংগতি তিনপ্রকার- (১) প্রগত স্বরসংগতি, (২) পরাগত স্বরসংগতি, এবং (৩) অন্যোন্য স্বরসংগতি।
প্রশ্ন ৩০ প্রগত স্বরসংগতি বলতে কী বোঝ?
উত্তর: পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনি বদলে গেলে তাকে প্রগত স্বরসংগতি বলে। যেমন- মিথ্যা > মিথ্যে, আ > এ; এভাবেই ‘ই’-এর প্রভাবে হিসাব > হিসেব, তিনটা > তিনটে ইত্যাদি।
প্রশ্ন ৩১ পরাগত স্বরসংগতি বলতে কী বোঝ?
উত্তর: পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি বদলে গেলে তাকে পরাগত স্বরসংগতি বলে। যেমন- দেশি > দিশি, পিছন > পেছন ইত্যাদি।
প্রশ্ন ৩২ অভিশ্রুতি কাকে বলে?
উত্তর: অপিনিহিতির ফলে পূর্বে আগত ‘ই-কার’ কিংবা ‘উ-কার’ যখন সন্নিহিত স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে, নিজেও তার সঙ্গে মিশে রূপান্তরিত হয়, তখন তাকে অভিশ্রুতি বলে। এক্ষেত্রে স্বরসংগতির প্রভাবও লক্ষ করা যায়। যেমন- করিয়া > কইরা > কইর্যা, রাতি > রাইত, রাত প্রভৃতি।
প্রশ্ন ৩৩ সমীভবনের সংজ্ঞা দাও।
উত্তর: কোনো শব্দের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্গের ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য দুটিকে একই বর্গের ধ্বনিতে রূপান্তরিত করা।
প্রশ্ন ৩৪ সমীভবন কতপ্রকার ও কী কী?
উত্তর: ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তনের অভিমুখ অনুসারে সমীভবন তিনপ্রকার-প্রগত, পরাগত এবং অন্যোন্য।
প্রশ্ন ৩৫ প্রগত সমীভবন বলতে কী বোঝ?
উত্তর: যে সমীভবনে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনিটি বদলে গিয়ে সমতাবিধান করে, তাকে প্রগত সমীভবন বলা হয়। যেমন-পক্ক > পক্ক, চক্র > চক্ক, পদ্ম > পদ্দ, চন্দন > চন্নন প্রভৃতি।
প্রশ্ন ৩৬ পরাগত সমীভবন বলতে কী বোঝ?
উত্তর: পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনিটি পালটে গিয়ে সমতা লাভ করলে তাকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন-গল্প > গল্প, পোদার > পোদ্দার, কপূর > কল্লুর, ধর্ম > ধম্ম, দুর্গা > দুয়া প্রভৃতি।
প্রশ্ন ৩৭ অন্যোন্য সমীভবন বলতে কী বোঝ?
উত্তর: পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে যখন উভয়েই পরিবর্তিত হয়, তখন তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে। যেমন-বৎসর > বচ্ছর, মহোৎসব > মোচ্ছব, উৎশ্বাস > উচ্ছ্বাস, কুৎসা > কেচ্ছা প্রভৃতি।
প্রশ্ন ৩৮ বিষমীভবন বলতে কী বোঝ?
উত্তর: সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া হল বিষমীভবন। কোনো শব্দের মধ্যে একইরকম ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সময় সেই ব্যঞ্জনধ্বনি যদি পালটে যায়, তবে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই রীতিকে বিষমীভবন বলা হয়। যেমন-লাল > নাল, শরীর > শরীল ইত্যাদি।
প্রশ্ন ৩৯ মহাপ্রাণীভবন বলতে কী বোঝ?
উত্তর: প্রতিটি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি এবং ঢ়, য়, ল, হ হল মহাপ্রাণ ধ্বনি। এই মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাবে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে মহাপ্রাণীভবন বলে। যেমন-বিবাহ > বিভাহ, লিচু > লিছু ইত্যাদি। একে পীনায়নও বলা হয়ে থাকে।
প্রশ্ন ৪০ অল্পপ্রাণীভবন বলতে কী বোঝ?
উত্তর: প্রতিটি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি এবং ড়, র হল অল্পপ্রাণ ধ্বনি। এই অল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রভাবে মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয় সেই প্রক্রিয়াকে অল্পপ্রাণীভবন বলে। যেমন-দুধ > দুদ, শৃঙ্খল > শেকল ইত্যাদি। একে ক্ষীণায়নও বলা হয়ে থাকে।
ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর
প্রশ্ন ৪১ মূর্ধন্যীভবন বলতে কী বোঝ?
উত্তর: শব্দমধ্যস্থ মূর্ধন্য ধ্বনির প্রভাবে সন্নিহিত দন্ত্যধ্বনি মূর্ধন্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে মূর্ধন্যীভবন বলে। যেমন- মৃত্তিকা > মাটি, বৃদ্ধ > বুড়া প্রভৃতি।
প্রশ্ন ৪২ উষ্মীভবন বলতে কী বোঝ?
উত্তর: স্পর্শধ্বনি উষ্ম ধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে উষ্মীভবন বলে। যেমন-মহাসুখ > মহাসুহ, কালীপুজা > খালীফুজা ইত্যাদি। এই ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন রাঢ়িতে তেমন লক্ষ করা যায় না।
প্রশ্ন ৪৩ নাসিক্যীভবন বলতে কী বোঝ?
উত্তর: শব্দমধ্যস্থ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি (ঙ, ঞ, ন ইত্যাদি) লুপ্ত হওয়ার ফলে তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিটি অনুনাসিক হয়ে যায়, এই প্রক্রিয়ার নাম নাসিক্যীভবন। যেমন-চন্দ্র > চাঁদ, হংস > হাঁস, দন্ত > দাঁত, চম্পা > চাঁপা, সন্ধ্যা > সাঁঝ ইত্যাদি।
প্রশ্ন ৪৪ স্বতোনাসিক্যীভবন বলতে কী বোঝ?
উত্তর: নাসিক্যধ্বনির প্রভাব ছাড়াই স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে গেলে তাকে স্বতোনাসিক্যীভবন বলে। যেমন-ঝাটা > ঝাঁটা, পেচা > পেঁচা, হাসপাতাল > হাঁসপাতাল ইত্যাদি।
প্রশ্ন ৪৫ স-কারীভবন বলতে কী বোঝ?
উত্তর: উষ্মীভবনের জন্য খৃষ্ট ধ্বনি চ, ছ, জ, ঝ যখন স্, শ্ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় তখন তাকে স-কারীভবন বলে। যেমন-খেয়েছে > খাইসে, গাছ > গাস, বলেছে > বলসে ইত্যাদি। বঙ্গালি উপভাষায় এই ধরনের রূপান্তর লক্ষ করা যায়।
প্রশ্ন ৪৬ র-কারীভবন বলতে কী বোঝ?
উত্তর: ‘স্’ ধ্বনির উচ্চারণ প্রথমে ‘জ’ এবং পরে বা শেষে ‘র’ ধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে র-কারীভবন বলে। যেমন-পঞ্চাদশ > পনেরো, দ্বাদশ > বারো।
প্রশ্ন ৪৭ অপিনিহিতি কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখো।
উত্তর: ‘অপি’ শব্দটির অর্থ পূর্বে এবং ‘নিহিতি’ তথা নিহিতের অর্থ সন্নিবেশ। অর্থাৎ অপিনিহিতির অর্থ পূর্বে সন্নিবেশ। শব্দের মধ্যস্থিত ‘ই-কার’ কিংবা ‘উ-কার’ স্বস্থানে থেকে অথবা স্বস্থান পরিবর্তন করে যদি অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আগে এসে উচ্চারিত হয়, তাহলে তাকে ধ্বনি পরিবর্তনের ভাষায় বলে অপিনিহিতি। পূর্ববঙ্গ বা অধুনা বাংলাদেশের কথ্য বাংলায় অপিনিহিতির বহুল প্রচলন দেখা যায়।
উদাহরণ: করিয়া > কইর্যা, সাধু > সাউধ, দেখিয়া > দেইখ্যা, কালি > কাইল, কন্যা > কইন্না, লক্ষ্য > লইল্থ প্রভৃতি।
প্রশ্ন ৪৮ ধ্বনিবিপর্যয় বা বর্ণবিপর্যয় বা বিপর্যাস বলতে কী বোঝ?
উত্তর: উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দমধ্যস্থ দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি যখন নিজেদের মধ্যে স্থান বদল করে উচ্চারিত হয়, তখন ধ্বনি পরিবর্তনের সেই নিয়মকে বলে ধ্বনিবিপর্যয় বা বর্ণবিপর্যয় বা বিপর্যাস। যেমন-বাতাসা > বাসাতা, পিশাচ > পিচাশ, রিশা > রিক্ষা, হ্রদ > হদ > দহ, জানালা > জালানা ইত্যাদি।
প্রশ্ন ৪৯: কুৎসিত > কুচ্ছিত এই ধ্বনি পরিবর্তনটি কোন ধরনের সমীভবন নির্দেশ করে?
উত্তর: এটি অন্যোন্য সমীভবন নির্দেশ করে।
প্রশ্ন ৫০: ‘পানিহাটি > পাইনহাটি > পেনেটি’ এই ধ্বনি পরিবর্তনটি কোন ধরনের?
উত্তর: এটি অপিনিহিতি নির্দেশ করে।
প্রশ্ন ৫১: ‘মর্দ > মরদ’ এই শব্দের মধ্যে ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ কোনটি?
উত্তর: এটি স্বরভক্তি নির্দেশ করে।
প্রশ্ন ৫২: ‘শৃগাল > শিয়াল’ এই শব্দের ধ্বনি পরিবর্তনটি কোন ধরনের?
উত্তর: এটি অন্ত্যস্বরাগম নির্দেশ করে।
প্রশ্ন ৫৩: ‘মুকুট > মুটুক’ এই শব্দের মধ্যে ধ্বনি পরিবর্তনের যে নিয়মটি কাজ করেছে, তা কী?
উত্তর: এটি বিপর্যাস নির্দেশ করে।
প্রশ্ন ৫৪: ‘বানর > বান্দর’ এই ধ্বনি পরিবর্তনটি কোন জাতীয় শ্রুতিধ্বনির অন্তর্গত?
উত্তর: এটি ক-শ্রুতির অন্তর্গত।
প্রশ্ন ৫৫: ‘পাঁচশো > পাঁশশো’ এই ধ্বনি পরিবর্তনে কোন নিয়ম অনুসৃত হয়েছে?
উত্তর: এটি পরাগত সমীভবন নির্দেশ করে।
প্রশ্ন ৫৬: ‘হ্রদ > দহ’ এই ধ্বনি পরিবর্তনটি কোন ধরনের?
উত্তর: এটি অপিনিহিতি নির্দেশ করে।
প্রশ্ন ৫৭: ‘চাকরি > চাকুরি’ এই ধ্বনি পরিবর্তনে কোন নিয়ম লক্ষ করা যায়?
উত্তর: এটি মধ্যস্বরাগম নির্দেশ করে।
প্রশ্ন ৫৮: ‘শহরে’ এই শব্দের ধ্বনি পরিবর্তনটি কোন ধরনের?
উত্তর: এটি অন্যোন্য স্বরসংগতি নির্দেশ করে।
প্রশ্ন ৫৯: ‘পাঁঠা > পাঁটা’ এই শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন কোন ধরনের?
উত্তর: এটি ক্ষীণায়ন নির্দেশ করে।
প্রশ্ন ৬০: ‘পা > ফড়িং’ এই শব্দের ধ্বনি পরিবর্তনটি কোন ধরনের?
উত্তর: এটি নাসিক্যীভবন নির্দেশ করে।
ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর
প্রশ্ন ৬১: ‘কালিপুজা > খালিফুজা’ এই ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন কোন উপভাষায় দেখা যায়?
উত্তর: এটি রাঢ়ি বঙ্গালিতে দেখা যায়।
প্রশ্ন ৬২: ‘খেয়েছে > খাইসে’ এবং ‘বলেছে > বলসে’ এই ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন কোন উপভাষায় প্রচলিত?
উত্তর: এটি রাঢ়ি বঙ্গালিতে প্রচলিত।
প্রশ্ন ৬৩: ‘পাশ্চাত্য > পাশ্চাত্য’ এই শব্দের মধ্যে কি ধ্বনি পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে?
উত্তর: এটি সমীভবন নির্দেশ করে।
প্রশ্ন ৬৪: ‘ঘণ্টা > গাঁথা’ এই ধ্বনি পরিবর্তনটির উদাহরণ কোন ধরনের?
উত্তর: এটি স্বরসংগতি নির্দেশ করে।
প্রশ্ন ৬৫: ‘ল’ কে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয় কেন?
উত্তর: ‘ল’ কে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয় কারণ শ্বাসবায়ু মুখবিবর থেকে নির্গত হয়ে এই ধ্বনিটি তৈরি হয়।
প্রশ্ন ৬৬: মৌলিক স্বরধ্বনি কী?
উত্তর: মৌলিক স্বরধ্বনি সেগুলি, যেগুলি বিশ্লেষণ বা বিভাজন করা যায় না, যেমন-অ, আ।
প্রশ্ন ৬৭: যৌগিক স্বরধ্বনির সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখো।
উত্তর: যৌগিক স্বরধ্বনি হল একটি মৌলিক স্বরধ্বনি এবং একটি অর্ধস্বরের মিলিত রূপ, যেমন-ও+ই = ঐ।
প্রশ্ন ৬৮: ঘোষীভবন ও উষ্ম ধ্বনি কী? উদাহরণ দিন।
উত্তর: ঘোষীভবন হলো ‘কাক’, ‘কাগ’; উষ্ম ধ্বনি হল শ, স, হ, য।
প্রশ্ন ৬৯: দীর্ঘস্বর কাকে বলে?
উত্তর: যে স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ করতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় লাগে, যেমন-আ, ঈ, উ।
প্রশ্ন ৭০: প্লুতস্বর কাকে বলে?
উত্তর: প্লুতস্বর হল যে স্বরধ্বনি দূরের কাউকে ডাকতে বা গান গাইতে প্রলম্বিত করে উচ্চারণ করা হয়, যেমন-রামু হে-এ-এ-এ।
প্রশ্ন ৭১: সংবৃত স্বর কাকে বলে?
উত্তর: সংবৃত স্বর হল যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট সংকুচিত হয়ে যায় এবং জিভ সামনে উঠে আসে, যেমন-ই, উ।
প্রশ্ন ৭২: বিবৃত স্বরধ্বনি কাকে বলে?
উত্তর: বিবৃত স্বরধ্বনি হল সেই স্বরধ্বনি, যখন মুখগহ্বর প্রসারিত হয়ে যায় এবং জিভ নিচে নেমে আসে, যেমন-আ।
প্রশ্ন ৭৩: উষ্ম ধ্বনি কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
উত্তর: উষ্ম ধ্বনি হল যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার পথ সঙ্কুচিত হয়, যেমন-শ, স, হ।
প্রশ্ন ৭৪: শিস্ ধ্বনিজাত ব্যঞ্জনের উদাহরণ দিন।
উত্তর: শিস্ ধ্বনিজাত ব্যঞ্জনের উদাহরণ হল-শ, য, স্, এবং হ।
প্রশ্ন ৭৫: তাড়নজাত বা তাড়িত ধ্বনি কী?
উত্তর: তাড়নজাত ধ্বনি হল যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু শুদ্ধভাবে সরে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি হয়, যেমন-ড়, ঢ।
প্রশ্ন ৭৬: কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনির উদাহরণ দিন।
উত্তর: ‘আ’ হল কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি, যেখানে জিভ আগু-পরু না হয়ে কেন্দ্রে থাকে।
প্রশ্ন ৭৭: স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি কী?
উত্তর: স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি হল যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু কিছু সময়ের জন্য মুখগহরের কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং জিভ উচ্চারণস্থানে স্পর্শ করে, যেমন-ক, খ।
প্রশ্ন ৭৮: দৃষ্ট বর্ণ বা ঘৃষ্ট ধ্বনি কী?
উত্তর: দৃষ্ট বর্ণ বা ঘৃষ্ট ধ্বনি হল যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের অগ্রভাগ তালুতে স্পর্শ করে, যেমন-চ, ছ।
প্রশ্ন ৭৯: ব্যল্গুনধ্বনি কী?
উত্তর: ব্যল্গুনধ্বনি হল যে ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে, যেমন- ক, খ।
প্রশ্ন ৮০: নীচের ধ্বনিগুলি উচ্চারণস্থান অনুযায়ী কী ধ্বনি নির্ধারণ করুন: জ, ধূ, হ, ল।
উত্তর: জ-তালব্য ব্যঞ্জন, ধূ-নাসিক্যী ব্যঞ্জন, হ- কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন, ল- পার্শ্বিক ব্যঞ্জন।
ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর
প্রশ্ন ৮১: হ্রস্বস্বর কী?
উত্তর: হ্রস্বস্বর হল যে স্বরধ্বনিগুলি কম সময়ে উচ্চারিত হয়, যেমন-অ, ই, উ।
প্রশ্ন ৮২: নাসিক্য বা অনুনাসিক ধ্বনি কী?
উত্তর: নাসিক্য ধ্বনি হল যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখগহ্বর এবং নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়, যেমন-ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।
প্রশ্ন ৮৩: অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি কী?
উত্তর: অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি হল যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু নির্গত হওয়ার পরিমাণ কম হয়, যেমন- ক, খ, ড়, র।
প্রশ্ন ৮৪ মহাপ্রাণ ধ্বনি কাকে বলে?
উত্তর: যে সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু বা প্রাণ নির্গত হওয়ার পরিমাণ বেশি, তাদের মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।
যেমন: স্পর্শব্যঞ্জনগুলি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি এবং ঢ়, য়, ল, হ।
প্রশ্ন ৮৫ পীনায়ন ও ক্ষীণায়নের পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।
উত্তর: মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাবে অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে পীনায়ন বা মহাপ্রাণীভবন বলা হয়। যেমন: কাঁটাল > কাঁঠাল, থুতু > থুথু।
অল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রভাবে মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হলে, তাকে ক্ষীণায়ন বা অল্পপ্রাণীভবন বলা হয়। যেমন: আঠা > আটা (‘ঠ’ মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণে হয়েছে অল্পপ্রাণ ধ্বনি ‘ট’), দেখছে > দেখচে, চোখ > চোক।
প্রশ্ন ৮৬ অঘোষ বর্ণ বা ধ্বনি কাকে বলে?
উত্তর: যে সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত ঘোষ বা সুর মিশে যায় না, তাদের অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। ‘ক’, ‘চ’ প্রভৃতি প্রতিটি বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি এবং শ, স হল অঘোষ ধ্বনি।
প্রশ্ন ৮৭ অঘোষীভবন কাকে বলে?
উত্তর: অঘোষ ধ্বনির প্রভাবে কোনো কোনো ঘোষ ধ্বনি যখন অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়, তখন তাকে অঘোষীভবন বলে। যেমন: কাগজ > কাগচ, বীজ > বিচি।
প্রশ্ন ৮৮ ঘোষীভবন কাকে বলে?
উত্তর: ঘোষ ধ্বনির প্রভাবে যখন অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, তখন তাকে ঘোষীভবন বলে। যেমন: কাক > কাগ, শাক > শাগ।
প্রশ্ন ৮৯ নাদ ধ্বনি বা ঘোষ ধ্বনি কাকে বলে?
উত্তর: যে সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত ঘোষ বা সুর মিশে যায়, তাদের ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। ‘গ’, ‘য়’ প্রভৃতি প্রতিটি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি এবং ‘র’, ‘ল’, ‘হ’, ‘ড়’, ‘ঢ়’, ‘য়’ হল ঘোষ ধ্বনি।
প্রশ্ন ৯০ তরল স্বর কাকে বলে?
উত্তর: তরল স্বর হলো যেসব ধ্বনির উচ্চারণে মুখের ভিতরের অঙ্গগুলো সহজে চলতে থাকে এবং শ্বাসবায়ু মুক্তভাবে প্রবাহিত হয়। উদাহরণ: ‘ল’।
প্রশ্ন ৯১ মৌলিক স্বরধ্বনি ক-টি ও কী কী?
উত্তর: বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি হল সাতটি: ‘অ’, ‘আ’, ‘ই’, ‘উ’, ‘এ’, ‘ও’, এবং ‘অ্যা’। তবে ‘অ্যা’ ধ্বনি লেখার কোনো আলাদা বর্ণ নেই।
প্রশ্ন ৯২ বাংলায় অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি কী কী?
উত্তর: বাংলায় অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনিগুলি হল ‘অ’ এবং ‘অ্যা’।
প্রশ্ন ৯৩ উষ্ম বর্ণগুলি কী কী?
উত্তর: ‘শ’, ‘য’, ‘স’, এবং ‘হ’ কে বলা হয় উষ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি বা উষ্ম বর্ণ।
প্রশ্ন ৯৪ মহাপ্রাণ ধ্বনির একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: মহাপ্রাণ ধ্বনির একটি উদাহরণ হল ‘খ’।
প্রশ্ন ৯৫ বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি কোনটি?
উত্তর: বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনিটি হল ‘আ’।
ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর
প্রশ্ন ৯৬ দুটি নাসিক্য ব্যঞ্জনের উদাহরণ দাও।
উত্তর: দুটি নাসিক্য ব্যঞ্জন হল ‘ঙ’ এবং ‘ঞ’।
প্রশ্ন ৯৭ ‘আ’-কে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি বলার কারণ কী?
উত্তর: ‘আ’ স্বরধ্বনিটি উচ্চারণ করার সময় জিভ আগুপিছু না-করে কেন্দ্রস্থলেই অনড় থাকে, তাই ‘আ’-কে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি বলা হয়।
প্রশ্ন ৯৮ ‘ঋ’-কে মিশ্র ধ্বনি বলা হয় কেন?
উত্তর: দন্তমূলীয় ব্যঞ্জনধ্বনি ‘র’-এর সঙ্গে উচ্চ স্বরধ্বনি ‘ই’ যোগ করে ‘ঋ’-এর উচ্চারণ করা হয়। বাংলায় ‘ঋ’-এর কোনো পৃথক উচ্চারণ নেই, তাই ‘ঋ’-কে মিশ্র ধ্বনি বলা হয়।
প্রশ্ন ৯৯ অবর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি কী কী?
উত্তর: অবর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি হল: য, র, ল, ব, শ, য, স, হ, জ, ই ইত্যাদি।
প্রশ্ন ১০০ আশ্রয়স্থানভাগী বা অযোগবাহ ধ্বনি কাকে বলে?
উত্তর: যে ধ্বনিগুলি অন্য কোনো স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনিকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়, তাদের অযোগবাহ ধ্বনি বা আশ্রয়স্থানভাগী ধ্বনি বলা হয়। যেমন: ং (অনুস্বর), ঃ (বিসর্গ)। এই দুটি ধ্বনির সঙ্গে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির কোনো যোগ নেই, তাই এরা অযোগবাহ।
প্রশ্ন ১০১ ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য কী?
উত্তর: ধ্বনি হল ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক, যা কেবল শোনা যায়, অন্যদিকে ধ্বনির লিখিত রূপ হল বর্ণ।
প্রশ্ন ১০২ অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যে স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ করার সময় ‘অ’ বা ‘অ্যা’-এর মতো অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের চেয়ে ঠোঁট দুটি কম খোলে, তাদের অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি বলা হয়।
উদাহরণ: এ, ও।
আরোও দেখো: রাজা রামমোহন রায় বায়োগ্রাফি